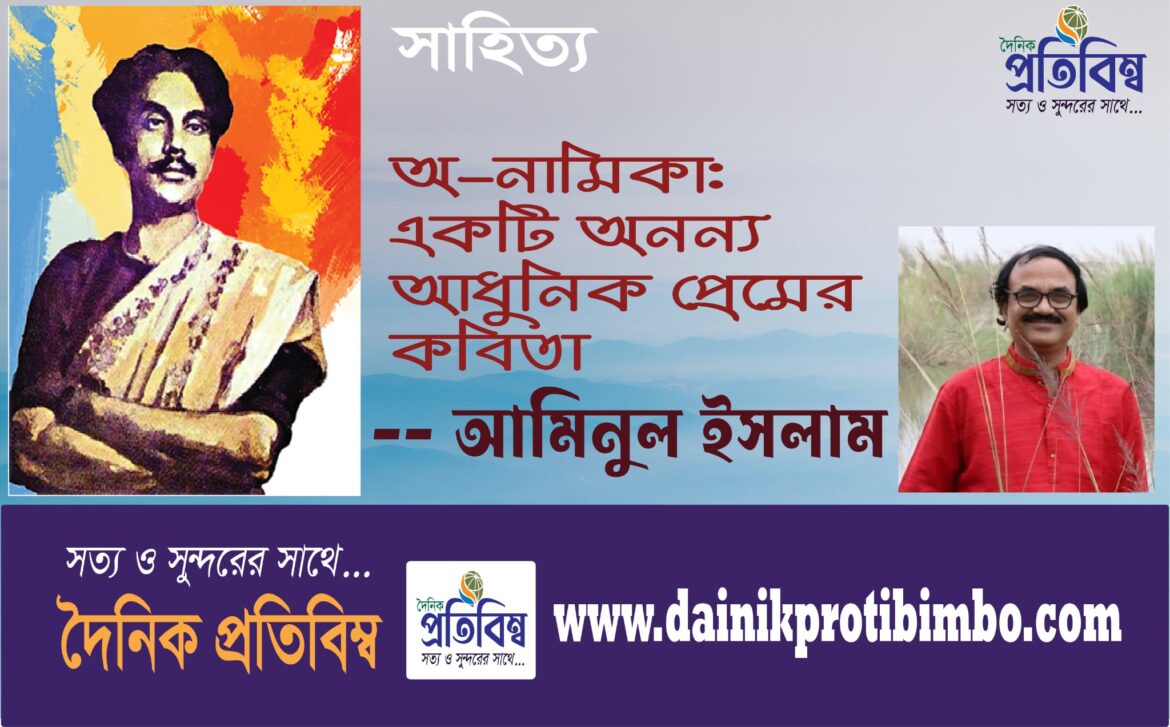৪২৬
সত্যিকারের আধুনিক মন সকল প্রকার কূপমণ্ডূকতার বিপরীতে
সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। কূপমণ্ডূকদের দাবির বিপরীতে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত আরবি ফারসি উর্দু ইংরেজি শব্দের সুষম ও জুতসই ব্যবহার ঘটিয়ে তাঁর কবিতা-গানকে অভিনবত্বে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এতে করে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাভাষার ভাণ্ডার। তাঁর সুপ্রচুর গজল গান এবং অজস্র কবিতা চিরসবুজ, সুন্দর , বৈশ্বিক ঘ্রাণে সুরভিত ও উপভোগ্যতায় অনন্য হয়ে উঠেছে ‘অ-নামিকা’ কবিতাতেও তাঁর সেই অবদান ও সাফল্যের সোনালি ছাপ পড়েছে।
অ-নামিকা’ : একটি অনন্য আধুনিক প্রেমের কবিতা
আমিনুল ইসলাম
আধুনিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্য থেকে দুভাবে আলাদা। বিষয় হিসেবে আধুনিক সাহিত্য অনেক বেশি ইনক্লুসিভ। জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর সাথে তার কদর্য বা নেতিবাচক দিকগুলোও এখানে সমহিমায় স্থান লাভ করে। অনেক সময় জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোই অধিক গুরুত্ব ও কদর পেয়ে থাকে। হতাশা, ব্যক্তি-যন্ত্রণা, নিবিড় নৈরাশ্য, সমকাম, পরকীয়া, পতিতাগমন-অভ্যাস, সমাজের প্রতি দায়দায়িত্বহীন মানসিকতা, তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা, সংশয় এসবই আধুনিক সাহিত্যের সোনালি উপকরণ। সেভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল ফরাসি কবি বোদলেয়ারের আধুনিক কাব্য ‘ক্লেদজ কুসুম’। অনুরূপভাবে আধুনিক সাহিত্য যুগপুরাতন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বৈষম্যমূলক প্রথা, মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ এসবকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলতে চায়। মুক্তমন ও মুক্তসমাজ আধুনিকতার দাবি। সাহিত্যে আধুনিকতার আরেকটি দিক হচ্ছে প্রকরণ বা আঙ্গিক। এটি সংহত, নিরাবেগ, অশিথিল, ইঙ্গিতময়, অপেক্ষাকৃত কম অলঙ্কারময় ও ব্যঞ্জনাগর্ভ । ভাবনায় যিনি আধুনিক নন, কেবল আধুনিক কাব্য আঙ্গিক অনুসরণ করে তার পক্ষে আধুনিক কবিতা রচনা সম্ভব নয়। আমরা সাহিত্যের আধুনিকতা বিচার করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় শুধু আঙ্গিকগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করি, দিকগুলো বিবেচনায় নেয়ার কথা ভুলে যাই। কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে মূল্যায়নের সময় এ বিষয়টি ঘটে এসেছে সবচেয়ে বেশি। নজরুল তাঁর সাহিত্যভাবনায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে একজন আলোকিত আধুনিক মানুষ।
আসলে নজরুলের সাহিত্যেই একটা সাহিত্যিক বিদ্রোহ ছিলো এবং প্রবলভাবেই ছিলো। সেটা মূলত অগ্রসর ভাবনার বিদ্রোহ বা আধুনিক ভাবনার বিদ্রোহ। নজরুলের কবিতাতে এবং গানে বুদ্ধদেব বসু কথিত ‘বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা’, ‘সংরাগের তীব্রতা’ এবং ‘জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন’ অত্যন্ত বেশি। নজরুল বাস্তবের মাটি ত্যাগ করে কল্পনার আকাশচারিতায় উড়ে যাননি। তিনিও উড়েছেন কিন্তু মাটির সাথে সম্পর্ক ছেদ করেননি। জীবনের জ্বালাযন্ত্রণাই তাঁর সৃষ্টির মূল প্রেরণা। তাঁর বিদ্রোহ আত্মিক ও সামষ্টিক যন্ত্রণারই উৎসারণ। তাঁর প্রেমভাবনাও হৃদয়িক যন্ত্রণায় রক্তাক্ত। তিরিশের পঞ্চপা-বের সাথে তাঁর মূলত পাথক্য কাব্যভাষার।
নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলোতে মানুষের হৃদয়ের চাহিদার পাশাপাশি শরীরের চাহিদাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা নজরুলের কবিতাতেই উঠে এসেছে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবের ঘনিষ্ঠতার বিবেচনাতেও নজরুলের সৃষ্টি নিবিড়ভাবে মাটিঘেঁষা। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলো ‘পূজারিণী’, ‘অ-নামিকা’,‘সিন্ধু’ ‘মাধবী-প্রলাপ’, ‘চক্রবাক’ একইসাথে বাস্তবতার ঘ্রাণ ও বেদনার ব্যঞ্জনায় ভরপুর। এখানে শুধু তাঁর ‘অ-নামিকা’ কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। তিনি ‘অ-নামিকা’ নামক কবিতায় এই কবিতায় প্রেম সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ সাহস নিয়ে বলেছেন, ‘জন্ম যার কামনার বীজে/ কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।’ প্রেমের জন্ম কামনায়? কাজী নজরুল ইসলাম সেকথাই তো জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি হৃদয়সর্বস্ব রোমান্টিকতাকে উড়িয়ে দিয়ে কবিতায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন রক্তমাংসে গড়া শারীরিক কামনা-বাসনার প্রবল অস্তিত্ব। তিনি মানুষের শারীরিক কামনা-বাসনাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রতিটি প্রাণে, প্রতিটি অস্তিত্বে, প্রতিটি পিপাসায়। প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলের জৈবিক সত্তার মূলে রয়েছে কাম বা যৌনচাহিদা, হৃদয়িক টানের সাথে মিশে রয়েছে শারীরিক তৃষ্ণা, সেটা তিনি প্রবলভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রেমের কবিতায়। ‘অ-নামিকা’-তেও। রোমান্টিক প্রেমের কবিতায় একটা অবাস্তব শুচিবায়ুগ্রস্ততা থাকে যে– প্রেমের মানুষটিকে কেবল হৃদয়ে আপন করে পেলেই চলে, তার শারীরিক সংসর্গের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাস্তবতা তেমনটি নয়। কিংবদন্তির লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট, চ-ীদাস-রজকিনী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ভালোবাসার মানুষটিকে শারীরিক সান্নিধ্যে পাওয়ার তীব্র বাসনা ও ঝুঁকিপূর্ণ সাধনা ছিল। শারীরিক চাহিদবিহীন দুটি মানুষের মাঝে বন্ধুত্ব হতে পারে কিন্তু প্রেম নয়। শুধুই দৈহিক পিপাসা প্রেম নয় আবার দেহের চাহিদাকে মাইনাস করে প্রেম এই বাস্তবতা বিরাজিত বিশ্বের সকল প্রাণীর মাঝে। রোমান্টিকদের চোখে শিল্পসাহিত্যে এই বাস্তবতার পক্ষাবলম্বন অনেকটাই দোষের, কিন্তু আধুনিকতার কাজ হচ্ছে তাকে স্বীকার করা এবং প্রয়োজনে মহিমান্বিত করা। কাজী নজরুল ইসলামের ‘অ-নামিকা’ কবিতার মাঝে আমরা আধুনিক প্রেমভাবনার দুরন্ত উদ্ভাসন দেখতে পাই।
‘তরু, লতা, পশু, পাখি, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে,–আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি-
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি,
তরুল-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!’
[অ-নামিকা, কাব্যগ্রন্থ: সিন্ধু হিন্দোল]
নজরুলের ‘অ-নামিকা’ কবিতা বিষয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এখানে কল্পনার প্রাধান্য অনেক বেশি যা সাধারণত রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। বাস্তবে ব্যাপারটা তেমন নয়। নজরুল নরনারীর মনোদৈহিক পিপাসা তাড়িত প্রেমকে ব্যাপক মাত্রা প্রদানের জন্য কবিতার নারী ‘অ-নামিকা’-কে দেখা-না দেখা, অতীতের-বর্তমানের, জন্ম নেয়া-জন্ম না নেয়া নারীর মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কল্পনাবিলাস নয়। বরং নজরুল তাঁর বাস্তবনিবিড় প্রেমভাবনাকে ব্যাপকভাবে এবং সকলের মাঝে সত্য করে তোলার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন।
‘প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র সত্য বগু-অগণন
তাই- চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!’
[পূর্বোক্ত]
উদ্ধৃত চরণসমূহের শেষের দুটির শেষে বিস্ময়-সংশয় চিহ্নের প্রেমভাবনাকে প্রশ্নবিজড়িত করে তার আধুনিক চারিত্র্যে বাড়তি ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। আসলে আধুনিক ভাবনা প্রায়শ অমিমাংসা ও সংশয়কে প্রশ্রয় দেয় এবং প্রশ্নশীলতার স্থান সৃষ্টি করে রাখে।
আধুনিক মানুষ মানেই বহুমাত্রিক মানুষ। লাইল-মজনুর প্রেমকে শ্রদ্ধা করলেও এ যুগের মানুষ সেই ‘আমরণ একনিষ্ঠ প্রেম ’ এর অনুসারী নয়। জীবনে একাধিকবার প্রেম আসতে পারে; একাধিক মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হতে পারে। এবং সেই সম্পর্ক শুধু হৃদয়কেন্দ্রিক পিপাসা বা নিষ্কাম প্রেম নয়, সেটা মনোদৈহিক যুগল চাহিদা। মানুষ আসলে অধিাকংশ ক্ষেত্রেই বহুচারী এবং বহুগামী। একজনের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হলে সেই ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবন পার করে দেওয়ার মানুষ কোনোদিনও বেশি ছিল না, আজো নেই। অনুরূপভাবে দুজন নর-নারী প্রেমবন্ধনে জড়িয়ে সংসার করতে করতেও অন্য মানুষের প্রেমে পড়েন এবং এমনটা কারো কারো ক্ষেত্রে বহুবারও ঘটে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে ও সংস্কৃতিতে এটা অনেক আগে থেকেই বহুল ঘটিত, বহুচর্চিত এবং অনিন্দিত ব্যাপার। বর্তমানে এটি এশিয়াতে বা আরও বৃহত্তর পরিসরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রবলভাবে ঘটমান ও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিজীবনেও একাধিক প্রেমের উঁকিঝুঁকি ছিল যদিও সেসব সফল হওয়ার মতো পরিণতি লাভ করেনি। নজরুল সেই সময়েই বহুমাত্রিক বহুরৈখিক বহুগতিক প্রেমের জয়গান গেয়েছেন যা সেই সময়ের কবিদের সাহসের পরিসীমার বাইরে ছিল বললেও চলে।
বাংলাভাষার প্রেমের কবিতা মূলত বিরহের কবিতা,– হাহাকারের কবিতা,— হা-হুতাশের কবিতা,– ভীরু ও হতোদ্দ্যোম মানুষের কবিতা,—এবং ঝুঁকি নিতে ব্যর্থ মানুষের অন্যপক্ষের ওপর ব্যর্থতার দোষারোপের কবিতা। বাংলার ভাষার প্রেমের কবিতা মূলত মিলনে ব্যর্থ হয়ে বিরহ উদযাপনের কবিতা। সেখানে যৌবন নেই, বীর্যবানতা নেই, প্রিয়জনকে জয় করে নেয়ার অ্যাডভেঞ্চার নেই । সেখানে যাপনের মধ্যে উপভোগের উচ্ছলতা নেই, আছে শরীরমনের যৌবনে জেগে উঠতে ব্যর্থ ও “ গাড়ি চলে না—চলে না—চলে না রে” প্রাণের যন্ত্রণা পোহানোর হীন মাতলামি। নজরুলের ‘অ-নামিকা’ প্রেমকে উপভোগ করতে প্রেরণা দেয়— পথ দেখায়। ধর্মগ্রন্থের বাণীকে মিথ হিসেবে ব্যবহার করে এ-কবিতা বলে যে স্রষ্টা রাগ করে নয়, অভিমান বশত নয়, প্রাণীকে জাহান্নামে পোড়ানোর অগ্নি-পরিকল্পনা থেকেও নয়, ভালোবেসেই সৃষ্টি করেছেন এই ভুবন—এই বিশ্ব—এই মহাবিশ্ব: ‘যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,/ সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।’ কারণ স্রষ্টা হচ্ছেন বিশ্বপ্রেমসত্তাময়। সেজন্যই তার সৃষ্টি সর্বত্র প্রেম বিরাজিত মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন যেটার নাম দিয়েছেন মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ। তাই একজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ মানে চিরকালের দেবদাস হয়ে থাকা প্রাণীর ধর্ম হতে পারে না। ‘অ-নামিকা’ হচ্ছে একজনকে নানাভাবে নানা পরিচয়ে নানান অনুষঙ্গে ভালোবাসার কবিতা— একইসঙ্গে নানাজনকে ভালোবাসারও কবিতা। এটা ভোগবাদিতা নয়, এর নাম উপভোগ। যারা ধর্ষক—যারা লুটেরা—যারার স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী—অন্যকে যন্ত্রণা দিয়ে তারা করে ভোগ, প্রেমিক-প্রেমিকা যা করে সেটা হচ্ছে পরস্পরকে অংশিজন বানিয়ে উপভোগ। “যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর”–পঙক্তির রচয়িতা কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “দুঃখবাদী” জীবনদর্শনের বিপরীতে ‘অ-নামিকা’-র নজরুলের সচ্ছল সবুজ-সতেজ প্রাণময় অবস্থান।
‘প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি’ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!’
[পূর্বোক্ত]
‘অ-নামিকা’ কবিতায় বিদ্রোহী কবির সৌন্দর্যচেতনা ফুটে উঠেছে প্রবল সুন্দরতায়। নজরুল রোমান্টিকদের মতো সবকিছুকেই সুন্দর দেখেননি। তিনি বোদলেয়ারদের ক্লেদজ কুসুমও দেখেছেন দৃষ্টির সমান নিবিড়িতায়। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে যাননি। তিনি সুন্দর সবকিছুকে ভালোবসেছেন আবার যা-কিছু সাধারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর নয় মর্মে প্রতীয়মান সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চোখে, তিনি সেসবকেও আপন হৃদয়ের রং ও চোখের আলো মিশিয়ে সুন্দর করে নিতে চেয়েছেন। আপন সুন্দর ও পর-সুন্দর একাকার সমগ্রতায় মিশে রচনা করেছে প্রেমময় সুন্দরের উঠোন।
যা-কিছু সুন্দর হেরি’ ক’রেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া ক’রেছি সুন্দর–
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!–ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে
প্রকাশ গোপন।
[পুর্বোক্ত ]
প্রেমভাবনার আধুনিকতার পাশাপাশি শব্দের জুতসই সাহসী ব্যবহার, চিত্রকল্পের অভিনবত্ব, উপস্থাপনায় নাটকীয়তা, ছন্দের লীলা এবং বাস্তবতা ও কল্পনার সমাবেশ প্রভৃতি ‘অ-নামিকা’ কবিতাটিকে একটি শিল্পসফল সৃষ্টিতে উন্নীত হতে সফল সহায়তা প্রদান করেছে। ‘ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলে না ক’ কথা কওয়া হ’য়ে।’, ‘তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় স’রে।’, ‘আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হ’য়ে নববধূ।’, ‘বুকে যারে পাই, হায়, / তারি বুকে তাহারি শয্যায়/ নাহি-পাওয়া’ হয়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,’, ‘দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে’, ‘লো আমার অনাগত প্রিয়া, / আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!’ ‘বাসনা-রঙ্গিনী’, ‘দ্রাক্ষা-বুক’, ‘সুদুরিকা’, ‘উতারো নেকার’–হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!’ ‘স্বপ্ন-সহচরী’, ‘তৃষ্ণা-জাগানিয়া’, ‘কান্ন-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া’, ‘চির-নাহি-আসা’, ‘যৌবন-ক্ষুধা’, ‘রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে’, ‘হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!’, ‘প্রেম-পাত্র বহু-আগণন’, ‘যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম’,‘ হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!’, ‘ছুঁয়েছি অধর তিলোত্তমা, তিলে তিলে!’, ‘গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!’, ‘দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব’, ‘সুদুরিকা! দূরে থাক’-ভালোবাসা-নিকটে এসো না।’, ‘উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা উদগ্র কামনা’, ‘তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে / আমার কামনা জাগে,-আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!’, ‘বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি’ / বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,/ হাওয়া-পরী / প্রিয় মনোরমা!], ‘বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি-/ সকলের মাঝে আমি-সকলের প্রেমে মোর গতি ‘, ‘যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,/ সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।’, ‘আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,/ বৃথা আমি খুঁজে মরি’ জন্মে জন্মে করিনু রোদন’, ‘বারে বারে পাইলাম-বারে বারে মন যেন কহে- / নহে, এ সে নহে! ‘, ‘ প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি, / চিনেছি তোমায়’, ‘তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়, / ভৃঙ্গারে, গোলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!’, ইত্যাদি শব্দ-সমাসবদ্ধ শব্দ-উপমা-চিত্রকল্প-কল্পচিত্র-বাক্যাংশ ‘অ-নামিকা’ কবিতাটিতে বহুমুখী ব্যঞ্জনা ও অনিঃশেষ সৌন্দর্যমাখা উপভোগ্যতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
সত্যিকারের আধুনিক মন সকল প্রকার কূপমণ্ডূকতার বিপরীতে
সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। কূপমণ্ডূকদের দাবির বিপরীতে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত আরবি ফারসি উর্দু ইংরেজি শব্দের সুষম ও জুতসই ব্যবহার ঘটিয়ে তাঁর কবিতা-গানকে অভিনবত্বে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এতে করে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাভাষার ভাণ্ডার। তাঁর সুপ্রচুর গজল গান এবং অজস্র কবিতা চিরসবুজ, সুন্দর , বৈশ্বিক ঘ্রাণে সুরভিত ও উপভোগ্যতায় অনন্য হয়ে উঠেছে ‘অ-নামিকা’ কবিতাতেও তাঁর সেই অবদান ও সাফল্যের সোনালি ছাপ পড়েছে।
‘দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে!-
‘উতারো নেকাব’-
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!
সুদুরিকা! দূরে থাক’-ভালোবাসা-নিকটে এসো না।’
[পূর্বোক্ত]
‘দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব’, চিত্রকল্পময় পঙক্তিটি যে সৌন্দর্য সুষমা ধারণ করেছে, সেখান থেকে ‘শিরীন্ শরাব’ শব্দদুটি প্রত্যাহার করে নিলে তার কবিতার খোলসে পর্যবসিত হয়ে যাবে। বঙ্গীয়-ভারত উপমহাদেশীয়-ইউরোপীয়-মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথ ও শব্দভাণ্ডার তাঁর দখলে ছিল। তিনি যখন যেমনটা সুপ্রযুক্ত তেমনভাবে শব্দ, মিথ ও উপমা নিয়ে কবিতা-গানের শরীর নির্মাণ ও প্রাণ সঞ্চার করেছেন। দেখা যাচ্ছে একই কবিতায় তিনি ভারত উপমহাদেশীয় মিথ এবং ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন জুতসইভাবে যা কবিতার সাবলীলতা ও সৌন্দর্য দু-ই বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি’
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয় মনোরমা!
ধরিতে গিয়েছি-তুমি মিলায়ে দূর দিগ্বলয়ে
ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলে না ক’ কথা কওয়া হ’য়ে।
‘পবনের যবনিকা’ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের একটি অবস্থার নাম । বায়ুমণ্ডল তথা বাতাসের একটি আবরণ থাকে যেটাকে পর্দা বললে বেশি স্পষ্ট হয়। এর কাজ হচ্ছে কোনোকিছুর দৃশ্যমানতাকে বাধা দেওয়া। প্রেমের পথে – প্রমাস্পদকে কাছে পাওয়ার পথে দৃশ্যমান বাধা ছাড়াও নানাবিধ অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতাও থাকে। এই কবিতায় প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার কারণ তুলে ধরার হয়নি। ‘পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!’—এই জাদুচরণ বা Magic line দিয়ে সৃষ্ট চিত্রকল্প সমস্ত অ-বলা ও অনির্বচনীয় প্রপঞ্চকে ধারণ করেছে কল্পযোগ্য রহস্যময়তায়। ‘ইন্দ্রধনু’ যেমন ভারতীয় মিথ, অনুরূপভাবে মধ্যাপ্রচ্যীয় কিংবদন্তি হচ্ছে ‘হাওয়া-পরী’। কবিতায় দুটোই সমানভাবে সুপ্রযুক্ত ও ব্যঞ্জনা বিকরণকারী।
কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের বাণীতে যতটা মহাবিশ্বের গগনবিদারী,—প্রেমের আলাপনে ততটাই সৃষ্টির অন্তরঙ্গ নিবিড়চারী। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ হচ্ছে সৃজনশীলতার পৃথিবীতে একটি হিমালয়– তাঁর ‘অ-নামিকা’ হচ্ছে একখানি তিলোত্তমা।
—–০০—–
ঢাকা: ২৭ অগাস্ট ২০২৫।