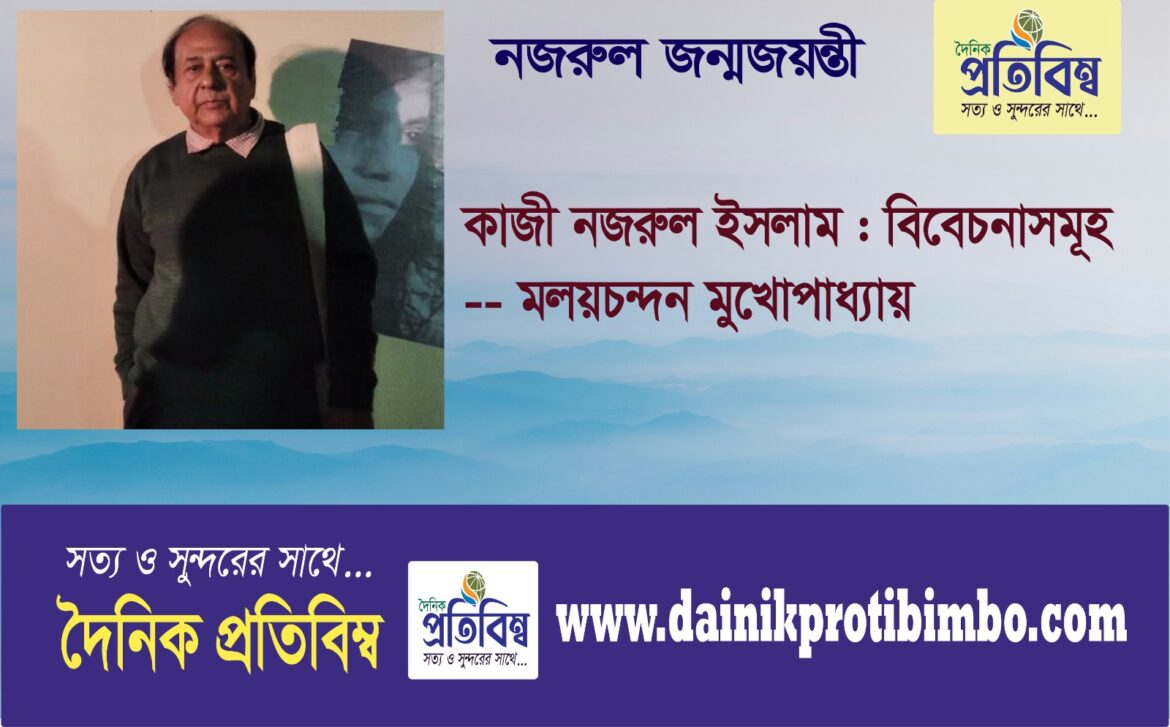কাজী নজরুল ইসলাম : বিবেচনাসমূহ।
— মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়।
প্রস্তাবনা।
সোয়াশো বছর বয়স অতিক্রম করলেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় চারদশকের ছোট, কিন্তু প্রতিস্পর্ধী এক প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যেতে পারে ‘ দুই ভ্রাতৃসূর্যলোক’।চুরুলিয়ার মত অজ্ঞানধূসর এক গ্রামে জন্মে, শৈশবে দারিদ্র্য, শৈশবে পিতৃহারা, শৈশবে জীবিকানির্বাহে নেমে পড়া, আর অনতিতিরিশে এই নজরুলকেই সম্বর্ধনা দেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকসভায় আগত তেইশ বছরের নজরুলকে মঞ্চে তাঁর পাশে ডেকে নিয়ে বসান ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ,যাঁর পাঁচ সন্তানের কনিষ্ঠটি, মীরা দেবীও নজরুলের চেয়ে সাত বছরের বড়ো,। পরের বছর নিজের লেখা ‘,বসন্ত’ গীতিনাট্য উপহার দেবেন তিনি নজরুলকে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩-এ এটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকে, আর নজরুল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা কবিতাসঙ্কলন” সঞ্চিতা’ উৎসর্গ করেন১৯২৮-এ।গুরুশিষ্যের সম্পর্কটি কেমন ব্যাকরণবহির্ভূত আর উদার নয়? এ নিয়ে সমালেচনা, নজরুল কি আদৌ কবি? প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নজরুলকে যারা কবি বলে মানেন না, তাদের নিজেদেরই কবিত্ব সম্পর্কে ধারণার অভাব।সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যখন তাঁরা যুদ্ধে যাবেন,( যুদ্ধে যাবেন, স্থির জানতেন তিনি ওই বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়েই!), তখন রণক্ষেত্রে তাঁর গান গাইবেন।এহেন নজরুল আজও কি আমাদের কাছে সম্যক প্রতিভাত? তাঁর মূল্যায়ন কি অদ্যাপি অন্ধের হস্তীদর্শনের মতই রয়ে যায় নি?
নানা নজরুলের মালা।।
কাজী নজরুলকে কবি বলে জানা তাঁকে নিতান্তই আংশিকভাবে জানা। তেমনি গীতিকার-সুরকার-গায়ক নজরুল -ও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।এই বহুমাত্রিক প্রতিভাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের একাধিক পরিমাপক লাগবে, যেমন লাগবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।বারবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রতিতুলনা আসে, কিন্তু এখন-ও তা যথার্থভাবে আসে না।রবীন্দ্রনাথ নি:সন্দেহে অনেক অনেক বড়ো প্রতিভা নজরুলের চেয়ে।তবে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র আছে,, যেখানে নজরুলকে এগিশে রাখতে হবে। কী সেগুলো? রবীন্দ্রনাথ বনাম নজরুল। একটি নিস্পৃহ অবলোকন।।
দুজনেই যুগন্ধর প্রতিভা, যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বহু বহু শতাব্দী।নজরুল আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে একজন মমুক্তমনা ও অসাম্প্রদায়িক। বারবার নজরুল হিন্দু -মুসলমানের ঐক্যের কথা বলেছেন, গদ্যে-পদ্যে- প্রবন্ধে।রবীন্দ্রনাথ -ও বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একসময় শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রাহ্মণ -অব্রাহ্মণের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন না, করজোড়ে নমস্কার করতেন। পরে এই নিয়ম তিনি তুলেও নিয়েছিলেন। এহেন বিচ্যুতি নজরুলের কখনো ঘটেনি।
রবীন্দ্রনাথ ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মে তিনি একেশ্বরবাদে আস্থাশীল ছিলেন, এবং মূর্তিপূজার বিরোধী। তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে, লক্ষ্মীর পরীক্ষা ‘ ‘ শারদোৎসব ‘ ‘ রথের রশি’, ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’। আবার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে,’অচলায়তন’ নাটকে,’বিসর্জন ‘ কাব্যনাট্যে।নিরাকারে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে সাকারবাদীও আবার, তাঁর সরস্বতীবন্দনার এই গানে,’এসো দেবী, এসো এ আলোকে,/ একবার তোরে হেরি চোখে,/গোপনে থেকোনা মনোলোকে/ ছায়াময় মায়াময় সাজে’। এসব তাঁর ধর্মীয়নসম্প্রসারের-ই পরিচয়। কিন্তু কী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে, কী শান্তিনিকেতন আশ্রমের মন্দিরের উপাসনা ও বক্তৃতায়, তিনি ব্রাহ্ম ঐতিহ্যকে সযত্নে বজায় রেখেছেন।
অন্যদিকে মুসলমান নজরুল তাঁর ধর্মীয় উদারতায় রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যান। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের কুসংস্কার ও কঠোরতাকে আঘাত করেন, ধর্মের প্রকৃত উদার দিককে তুলে ধরেন তাঁর লেখায়। ইসলামী সংগীত আর শ্যামাসঙ্গীত সমানভাবে প্রশ্রয় পায় তাঁর গানে।শ্যামাসঙ্গীত, মজার কথা, রবীন্দ্রনাথ -ও লিখেছেন। ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ নৃত্যনাট্যে ‘ রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা’। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন, একথা কেউ মনে রাখে না।অথচ নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত তাঁর সঙ্গীতজীবনের পাদপূরণ রূপে নয়, মধ্যবর্তী এবং কাব্যগুণসম্পন্ন।এই তিনিই আবার আমপারা লেখেন, হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ কে নিয়ে ‘ মরুভাস্কর’ রচনা করেন, যদিও দুর্ভাগ্য, এটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।নজরুল যেভাবে ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করেছেন, বেপরোয়া হয়েছেন সেইসঙ্গে,( আমি ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন ‘), তা কেবল বাংলাসাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেই তুলনাহীন। আধুনিকতার বিচারে এদেশের কবি মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ, বিদেশে এলিয়ট-ইয়েটস-এজরা পাউন্ডের তুলনায় নজরুল বেশ কয়েক কদম এগিয়ে। লেটোর দলে থাকতেই তিনি’শকুনি বধ’, ” রাজা যুধিষ্ঠির ‘, ‘ দাতাকর্ণ’, ‘কবি কালিদাস’ লেখেন। পরিণত বয়সে মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ করেন ওমরখৈয়াম আর হাফেজ।তাঁর লেখায় হিন্দু পুরাণের অনুষঙ্গ তো সলমা-চুমকির মত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।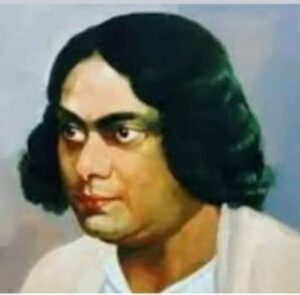
‘ আমরা এক-ই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান’, বেশ। কিন্তু বাকিরা? এ-ও যে তাঁর বিবেচনায় ছিল, তার প্রমাণ এই লেখায়, যে লেখার শিরোনাম ‘মানুষ’। সেখানে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা আনলেন, সেইসঙ্গে বিশ্বমানবতার। ‘আদম দাউদ ঈশা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ,/ কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, – বিশ্বের সম্পদ/ আমাদের এরা পিতা-পিতামহ,এই আমাদের মাঝে/ তাদেরি রক্ত কমবেশি করে প্রতি ধমনীতে বাজে।’ এই বিশ্বধর্মৈক্যবোধ রবীন্দ্রনাথে আছে কি?বুদ্ধ নানক কবীর, ঈশাকে বিশ্বের সম্পদ মনে করলেও তার আওতায় কৃষ্ণ, মোহাম্মদ বা ইব্রাহিমকে আনতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। মুসলমান নজরুলের পুত্রদের নাম এজন্যই হতে পারে কৃষ্ণ, অরিন্দম, সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ।
এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আর তাকে নিজ রচনায় বিপুলভাবে স্থান দেওয়ার মধ্যে বার্তা কী দিতে চান নজরুল? বার্তা একটি-ই, এ দুইকে মেলানো।এজন্য তাঁকে কঠিন, সুকঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।উদাহরণ, যে ‘প্রবাসী’ তাঁর লেখা ছাপতো নিয়মিত, প্রমীলার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর সেই পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নজরুলকে ব্রাত্য করে দিলেন। অসহিষ্ণুতা! প্রমীলা ছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। ব্রাহ্ম রামানন্দ তাই এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সীতা দেবী যাঁকে বিয়ে করেছিলেন সেই পাত্র সুবীর কুমার রায়চৌধুরী তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলেন। প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি এ বিয়েতে মত দেন। কিন্তু তাঁর উদারতা নজরুল পর্যন্ত এগোতে পারে নি! রামানন্দ -সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ কি এ জট ছাড়ানোর প্রয়াস নিয়েছিলেন? ইতিহাস নীরব।
নজরুল হাফেজ, ওমরখৈয়াম অনুবাদ করেছেন।অনুবাদকরূপে রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ একটি স্তান আছে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ম্যাকবেথ অনুবাদ করার দু:সাহস দেখান। ‘রূপান্তর ‘ গ্রন্থ টি তাঁর করা দেশি-বিদেশি কবিতার অনুবাদ-সঙ্কলন।হিন্দি, মারাঠী থেকে যেমন, তেমনি তিনি অনুবাদ করেছেন ভিক্টর হিউগো, গ্যয়টে, হেল্ডারলীন থেকে। তিনি কিন্তু কোনো ফর্সি কবিতার অনুবাদ করেন নি। সরাসরি না করতে পারলেও ইংরেজি থেকে করতে পারতেন। এর কারণ গভীরে। কৈশোরে পিতার সঙ্গে হিমালয়বাসে পিতা তাঁকে হাফেজ শোনাতেন।পরিণত বয়সে তিনি পারস্যেও যান।এবং হাফেজ ও সাদির কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন।এর আগে সিঙ্গাপুর ভ্রমণকালে সেখানকার এক পার্শি পরিবারের মহিলাদের কাছে তিনি তিরস্কৃত হন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাই, এর কারণ ছিল, সেই মহিলারা ভাবতেই পারেন না, যিনি কবি, তা যে দেশের-ই কবি হোন, ফার্সি জানেন না।
আসলে ঔপনিবেশিকতা আমাদের কেবল পাশ্চাত্যমুখী করে তুলেছিল। আমরা ইংরেজি সাহিত্য, সেইসঙ্গে ইয়োরোপীয় সভ্যতা নিয়ে কৌতূহলী হতে শিখেছি।একজন শিক্ষিত মানুষ শেকসপিয়ার পড়বে, শেলি কীটস বায়রন পড়বে,যেমন পড়বে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস। কিন্তু ফেরদৌসী, সাদি, রুমি আর ওমরখৈয়াম না পড়লেও যে যথাযথ সাহিত্যপাঠে খামতি থাকে, সে বোধ তৈরি হয়নি ঔপনিবেশিক ভারতে। রবীন্দ্রনাথ এই ঔপনিবেশিকতার ঊর্ধ্বে নন। নজরুল এইখানে একধাপ এগিয়ে।দেবেন্দ্রনাথের ফার্সিতে ব্যুৎপত্তি ছিল। তবু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার উত্তরাধিকার আশানুরূপ বর্তায় নি। নজরুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্তেছে।
রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল, দুজনেই ছিলেন পত্রিকা -সম্পাদক। জীবনের নানা পর্বে রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’,’ভাণ্ডার’,’ ”বঙ্গদর্শন ‘ ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
নজরুল -ও সম্পাদক ছিলেন’লাঙল’, ‘ধূমকেতু’,’ নবযুগ’ প্রভৃতি পত্রিকার। তবে নজরুলের যে সাংবাদিক -সত্তা, তা রবীন্দ্রনাথের ছিল না।রবীন্দ্র -সম্পাদিত পত্রিকা মূলত ছিল সাহিত্যের, আর নজরুলের পত্রিকাগুলিতে রাজনীতির ঠাঁই ছিল ব্যাপক।এজন্য বহু রাজনৈতিক মতামত, যা তখনকার ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে অনভিপ্রেত ছিল, বলিষ্ঠতার সঙ্গে তা প্রকাশ করতে নজরুল দ্বিধা করেন নি। এজন্য তাকে কারাগারেও যেতে হয়েছে। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর পাঁচ পাঁচটি গ্রন্থ।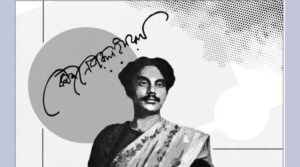
অন্যান্য অনেককিছুর মতই নজরুল আমাদের আরবি-ফার্সি সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর লেখাতেও বহু আরবি-ফার্সি শব্দের ছড়াছড়ি। শব্দগুলি বাংলা সাহিত্যকে আরো অনেক মজবুত করেছে। আমরা জানি, পৃথিবীতে যেসব ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ আত্মসাত করে নিজভাষার অধিগত করে, সেই সেই ভাষা ততো শক্তিশালী হয়। ইংরেজি ভাষা যে কারণে এতো শক্তিশালী ও আবিশ্বে গ্রহণযেগ্যতা পেয়েছে। নজরুলের এই শব্দধানুকী দিকটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা অপেক্ষিত রয়ে গেছে।আরবি-ফার্সি শব্দকে বাংলাভাষায় নিয়ে আসার প্রকৃত ভগীরথ নজরুল। মুকুন্দরাম-বিজয়গুপ্ত-ভারতচন্দ্রে(ভারতচন্দ্র তো ফার্সি জানতেন উত্তম), মাইকেল-রবীন্দ্রনাথে আরবি-ফার্সি শব্দ আছে অনেক, কিন্তু তা সহজাত। উদ্দেশ্যমূলকভাবে, বাংলাভাষার মধ্যে আরবি-ফার্সির বহুল ও মোক্ষম স্রোত বহানোর ব্রত নেন নজরুল -ই।
সেইসূত্রে মনে পড়বে তাঁর গানে নজরুল এনেছেন, আরবি-উৎস ও ইরানে লালিত-বর্ধিত গজল।উর্দুতে এ জিনিশ ছিল, বাংলায় নয়, নজরুলের আগে নয়। এর সঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা জরুরি। নজরুল অসংখ্য গানে নিজ-উদ্ভাবিত সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সুরসাধনায় একদিকে ভারতীয় মার্গসংগীত, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত, দেশীয় হরেক সুরকে ভেঙে, নেড়েচেড়ে, মিশ্রণ ঘটিয়ে তুলকালাম করেছেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেন রামপ্রসাদী, বাউল থেকেও
নজরুল-ও।নজরুলের গজল, রবীন্দ্রনাথের টপ্পার মতোই বাংলা গানে সংযোজন। ইসলামী গানে রবীন্দ্রনাথ নেই।গজল অবশ্য কিছু আছে,’এসো শ্যামল সুন্দর ‘ ইত্যাদি গানে। রবীন্দ্রনাথের ইসলামী গান না লেখার কারণ? ওই যে!-ঔপনিবেশিকতা!
নজরুলের বাংলা ও বাঙালি নজরুল।।
‘নমো নমো নমো বাংলাদেশ মম, চির মনোরম, চিরমধুর’, লিখেছিলেন নজরুল। কবিতাটিতে ষড়ঋতুর সুন্দর -শোভন বর্ণনা আছে, আছে নদী-সমুদ্র-ফলফুলের কথা।তাঁর বাংলা ফাগুনে ফুলবধূর সাজ পরে, আর ‘শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে/ গাহিয়া আগমনী গীতিবিধূর।’ ব্যক্তিগতভাবে তিনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার যে যে স্থানে গেছেন, কোথাও তাঁর পরবাস মনে হয় নি। রাঢ়ের মানুষটি বাঙ্গাল দেশেও সমান সহজ, সাবলীল, ও মনে হয় যেন সেখানকারই ভূমিপুত্র তিনি। তাঁর ঢাকার জীবন আর মেদিনীপুরের,নদীয়া( কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর) আর সিলেট-কুমিল্লা-চট্টগ্রামের, সবেতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি।তাঁর বাঙালিত্ব এখানেই দৃঢ় ও প্রকট। কোথাও তিনি অতিথি ও আগন্তুক নন, যেখানেই গেছেন, সেখানকারই ভূমিপুত্র মনে হয় তাঁকে। মেশেন, থাকেন অনির্দিষ্টকালের জন্য, গভীরভাবে আপন করে নেন সেখানকার লোকজনকে।বাঁকুড়া র দলমাদল কামানকে জড়িয়ে ধরে তাঁর যে ছবি, তাতে তো তাঁকে বাঁকুড়ার মানুষ বলেই প্রত্যয় হয়। আবার চট্টগ্রামে বসে তিনি যখন লেখেন,’আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাঙা আমার তরী’, তখন তিনি আকৈশোর যেন চট্টগ্রামের, যেন সাম্পানের মাঝি, এমনটাই মনে হয় না কি? এই যে প্রবলভাবে মিশে যাওয়া জনপদ ও জনপদবাসীর সঙ্গে, এ নজরুলের একান্ত গ্রহণক্ষমতাজাত সপ্রাণতা। অন্যদিকে কীটস-কথিত ‘Negative capibility’- ও বটে এসব বিবেচনায় নজরুলকে অসীম গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ রূপে কুর্নিশ জানাতে হয়। তিনি বাংলার বাইরে, বিদেশ তো দূরের কথা, উপমহাদেশেও বিশেষ যান নি। সৈনিক হিসেবে করাচি, ব্যস। না দিল্লি আগ্রা লক্ষ্ণৌ, না কাশ্মীর রাজস্থান পাঞ্জাব।অসুস্থ নজরুল রাঁচি গেছিলেন চিকিৎসা করাতে। গেছেন ইংল্যান্ড, জার্মানি। সেসব’ যাওয়া তো নয় যাওয়া।’ তাঁর সমসাময়িক জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, বা পরবর্তীকালের সুকান্তর চেয়েও নজরুলের ভ্রমণপরিধি সীমায়িত। তাঁর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল যে জসীমউদ্দিনের, তিনিও ইয়োরোপ-আমেরিকা গেছেন। নজরুলের ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারলে আমরা আরো এক সমৃদ্ধ নজরুলকে পেতে পারতাম। তবু, যে বলয়টুকুতে তিনি পরিক্রমা করেছেন, তাকে পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যে এনে সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যকে।আর একথাও মনে রাখা দরকার, এই বাংলার ছোট গণ্ডিতে বসেই বিশ্বকে দেখেছেব তিনি, আন্তর্জাতিক কোনো ঘটনাই তাঁর নজর এড়ায় নি, বা তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে তিনি ছাড়েন নি।
নজরুলের সঙ্গে ছায়াছবির যোগটিও ছিল ব্যাপ্ত।নিজে যেমন চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন(‘ধূপছায়া’), তেমনি একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। সঙ্গীতপরিচালক রূপে ও তাঁকে দেখি”জামাইষষ্ঠী’,’ গ্রহের ফের’,’ পাতালপুরী’,’ গোরা’,’ রজতজয়ন্তী ‘,’ অভিনয় ‘,’ দিকশূল ‘ ‘গৃহদাহ’, ,’ চৌরঙ্গী ‘(এটি বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষিক ছবি। ছবিটির জন্য সাতটি হিন্দি গান-ও লিখতে হয়েছিল তাঁকে)।কাহিনীকার ছিলেন’সাপুড়ে’ ছবির। তবু দারিদ্র্য ঘোচে নি তাঁর। কেননা সর্বত্র তিনি বঞ্চিত -শোষিত হন।ভাবা যায়, গ্রমোফোন কোম্পানির শিক্ষক নজরুল জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেকর্ড বিক্রি করছেন! অন্যদিকে তাঁর স্বভাব- ঔদাসীন্যের কারণে তাঁর লেখা বহু গান আত্মসাৎ করেছেন কতো (অ)মানুষ! মাত্র একুশ বছর বয়স থেকেই গানরচনার শুভ সূচনা তাঁর। ১৯২০-তে তাঁর লেখা প্রথম যে গানটি ‘সওগাত’ পত্রিকায় বেরোয়, সেটি হলো’ বাজাও প্রভু বাজাও ঘন’।অবশ্য তার আগেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনী সেনগুপ্ত নজরুলের কবিতায় সুর দিয়ে স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছিলেন।
নাম ছিল দুখু মিয়া। বাস্তবেও তাই। তাঁর জন্মের ন’বছরের মাথায় বাবা মারা যান। মা আবার বিয়ে করেন। নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল কিনা সুনিশ্চিত নয়, তবে বিয়ের রাতেই নাটকীয়ভাবে পালাতে হয় তাঁকে। তাঁর লেখা একের পর এক বই বাজেয়াপ্ত হয়। বিয়ের পর বছরের পর বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রবল লড়াই করতে হয়, আর এর মধ্যেই লিখে চলেন একটির পর একটি অবিস্মরণীয় কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কী নয়? শাশুড়ি সহসা নিরুদ্দেশ! তেতাল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ চিরতরে বাক্ রুদ্ধ! তার আগেই স্ত্রী প্রমীলা পক্ষাঘাতগ্রস্ত! ১৯৬২-তে নজরুলকে ওই অবস্থায় রেখে প্রমীলার মৃত্যু। নাবালক দুই পুত্র, কী খাবেন, পরবেন, পড়ালেখা করাবেন স্থিরতা নেই! তবুএ আজীবন, যতদিন সচেতন ছিলেন, সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই ছিলেন, জাহান্নামের আগুনে বসে পুষ্পের হাসি হেসে গেছেন।
নজরুলের সমগ্র সাহিত্যজীবন কোন অভীপ্সা ও দর্শনের দ্বারা চালিত হয়েছিল? এর উত্তর নিহিত আছে তাঁর নিজের-ই উক্তিতে,’ আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবানকর্তৃক প্রেরিত।কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন।আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়।আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে'(রাজবন্দীর জবানবন্দী)।
নজরুলকে নিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা আমাদের, যা মিটবে অনবরত তাঁর লেখা পড়লে, তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা করলে। সমসাময়িক জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর কি যোগাযোগ ছিল? সুকান্ড, মানিক, বিভূতিভূষণ, বা অন্যন্য লেখকরা কেন তাঁর সম্পর্কে নীরব, তখনকার বহু বিখ্যাত গত্রিকা তাঁর লেখা ছাপে নি কেন, এরকম প্রশ্নের মীমাংসা চাই। তিরিশের দশকে নজরুল প্রবলভাবে সক্রিয়। অথচ তখনকার কবি সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে বা সমর সেন- সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে কিছুই লিখলেন না কেন( একমাত্র ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসু। তিনি নজরুলকে নিয়ে স্বসম্পাদিত ‘,কবিতা ‘-র একটি সংখ্যাও বের করেছিলেন)? এখনো জানি না আমরা।
পুরস্কার জীবনে কম পান নি তিনি, যা প্রধানত অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু। এবং মৃত্যুর পরেও। ১৯৪৫-এ পেলেন জগত্তারিণী, ‘৬০-এ পদ্মভূষণ। ১৯৭৪-এ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে’জাতীয় কবি’ ঘোষণা করে, যা আইনগতভাবে কার্যকর হয় ২০২৪ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪-এ তাঁকে ডি লিট দেয়।১৯৭৬-এ তাঁকে দেওয়া হয় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব। সে বছর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে।১৯৭৭-এ তিনি পান মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক।কিন্তু এসব পুরস্কারের বার্তা তাঁর বোধগম্য হয় নি!
রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নজরুলকে নিয়ে, শেলী ও কীটস-এর মতো তাঁর জীবনেও ট্র্যাজেডি আসবে। তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর সমগ্র লেখার মাধ্যমে? এজন্যই কি তিনি আগাম লিখে গিয়েছিলেন,’ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি’? আমরা জানি না, কেন না রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মতো আমরা কবি ও ত্রিকালজ্ঞ নই।