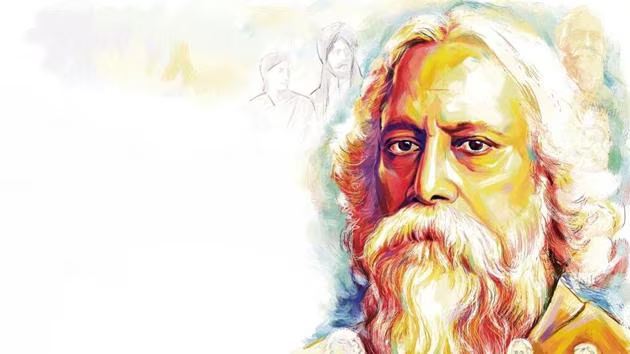৩৪২
কবির কন্ঠস্বর
জুলফিকার নিউটন
কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে-লক্ষ্য করার বিষয় যে কবি এ কথা বলেছেন তিনিও নিজেই নিজের জীবনচরিত লিখেছেন। অবশ্য সে জীবনচরিত গতানুগতিক জীবনী কাহিনী নয়। সেখানে স্থান কাল সন তারিখের ভিড় নেই অর্থাৎ জিনিসটা নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। কবি সাহিত্যিকের জীবনে ঘটনার ভূমিকা খুব বড় নয়। ঘটনার একটা চাক্ষুষ মূর্তি আছে। সে তার চতুর্পাশে চাঞ্চল্যের ঢেউ তোলে, সরবে নিজেকে ঘোষণা করে, নানা ভাবে নিজেকে জাজ্জ্বল্যমান করে তোলে। যে মানুষ কর্মী তাঁর জীবনে সেটা এক রকম মানিয়ে যায়-সেখানে ছোট বড় সব ব্যাপারই শোরগোল করে ঘটে। কিন্তু যে মানুষ ভাবুক প্রকৃতির, তাঁর জীবনে কোনো কিছুই ঘটা করে ঘটে না। বিশেষ করে কবির মন একটা অদ্ভুত আঁধার-সব জিনিসকে সে গ্রহণ করে না। ছাঁকনির ফাঁক দিয়ে অনেক বৃহৎ ঘটনাও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলে ঝরে যায়; আবার অনেক ক্ষুদ্রে জিনিস চিরকারের জন্য মনের তারে বাধা পড়ে যায়। মনের তারে যে জিনিস ঝংকার তোলে তাকে ঘটনা বলতে হয় বলুন, কিন্তু সে ঘটনার স্বভাব অন্যরূপ। কবির জীবনে ঘটনা বলতে দুটি-একটি সুন্দরের অনুভূতি, অপরটি সুন্দরের প্রকাশ। ঘটনা হলেও এরা উভয়েই নম্রস্বভাবী। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সংসারের পরমাশ্চর্য ঘটনাগুলি পরম নিঃশব্দে ঘটে। শোরগোল করে ঘটে না বলে সহজে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যিনি প্রধানতঃ মননের জীবন যাপন করেন তাঁর জীবনের বহিরঙ্গের বহরটা খুব বড় নয়। সে জন্য কবির জীবনী রচনা করা কখনই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে যা ঘটেছে এবং তার প্রসাদ যিনি অন্তরে লাভ করেছেন নিজ মুখে ব্যক্ত না করলে তা জানার উপায় থাকে না।
দুঃখের বিষয় হচ্ছে খুব কম কবিই এ কাজটি করে গেছেন। নিজে যা করেন নি অপরের তা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছে উল্টা এবং সেই কারণেই অনুমান করা যায় কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে-এ কথা শুধু রবীন্দ্রনাথের নয় সকল কবিরই মনের কথা। কবির জীবন অন্তর্মূখীন, সে কখনই খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। জীবনীকাররা এখানেই ভূল করেন। স্থান কাল বংপরিচয়ের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুস্পষ্ট-সীমানার মধ্যে জীবনটিকে তাঁরা বাঁধতে চান। এর ফলে দেখা গিয়েছে কবি মানুষের জীবনী-অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কথাটা শুনতে আপাতবিরোধী হলেও বলব, এই অতি-স্পষ্টতার দরুণই কবির কবিস্বভাবটি ঢাকা পড়ে যায়। সেখানে কবির লৌকিক জীবনের পরিচয় যদিবা পাওয়া যায়, কাব্যজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। টমসন লিখিত কবির জীবনী যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখেছিলেন, টমসন তাাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়-রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সেই অতিস্ফূটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষেল কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে, তাহার সম্বন্ধ আছে-সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি নির্দিষ্ট নহে। আমার সেই সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান নাই।
যিনি যত কবি তিনি তত বড় রহস্য-আমাদের কাছে তাঁর জীবন তত বেশি অস্পষ্ট। কারণ তিনি নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন, বাইরে বহুলাংশে অপ্রকাশিত। প্রাচীন যুগের মহা কবিদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তাঁদের জীবন কাহিনী কিংবদন্তীর বিষয়ীভূত। আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেকসপীয়র। এ কালের সকল কবি সাহিত্যিকের তুলনায় তাঁর জীবন সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান স্বল্পতম। এলিজাবেথীয় যুগের ইতিহাস নিয়ে কত মোটা মোটা গ্রন্থ রচনা হল, ছোট বড় মাঝারি কত মানুষের কাহিনী লেখা হল, কিন্তু সে যুগের যিনি মহত্তম পুরুষ, বৃহত্তম বিস্ময় তাঁরই কাহিনী অজ্ঞাত থেকে গেল। ইতিহাসের ছাঁকনির ফাঁক দিয়ে গলে যায়। ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিওপেট্রার স্বভাব বড় প্রগলভ, তিনি হাক ডাক জাঁক ভালবাসেন।
ইতিহাস রসের কারবারি নয়। ইতিহাস যাকে তুচ্ছজ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, রসিক চিত্ত তাকে অগ্রাহ্য করে না। কবির জীবনে সামান্যর স্থান অসামান্য এবং বৃহতের স্থান নগণ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের prelude কাব্যগ্রন্থ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলা বাহুল্য এই জীবনীকে কেউ ঘটনাপঞ্জী বলবে না। prelude এর অপর নাম The grouwthe of poetic mind–এটিই উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত নামকরণ। কবি- মনের গঠনে কোন্ ঘটনার কতখানি গুরুত্ব তা একমাত্র কবিই যথাযথ বলতে পারেন। আর কিঞ্চিৎ পারেন তেমন রসজ্ঞ এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনীকার যদি পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের কবি যেমন বিরল, যথার্থ রসজ্ঞ জীবনীকার বোধ করি ততধিক বিরল। এখানে বলে নেয়া ভালো যে, কবির জীবনে বৃহৎ ঘটনার কোনোই প্রভাব নেই এমন কথাও সরাসরি বলা চলে না। কবির আপন জীবনে অথবা তাঁর সমকালীন সমাজজীবনে এবং জাতির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে পারে যা কবির মনে নিঃসন্দেহে গভীর রেখাপাত করেছে। আসল প্রতিপাদ্য কথাটা হল কবি এবং কাব্য অবিচ্ছিন্ন। কবির জীবনের বৃহৎ ঘটনার কোনই প্রভাব নেই এমন কথাও সরাসরি বলা চলে না। কবির আপন জীবনে অথবা তাঁর সমকালীন সমাজজীবনে এবং জাতির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটনা ঘটতে পারে যা কবির মনে নিঃসন্দেহে গভীর রেখাপাত করেছে। আসল প্রতিপাদ্য কথাটা হল কবি এবং কাব্য অবিচ্ছিন্ন। কবির জীবনের মধ্যেই কাব্যকে খুঁজতে হবে। কবিকে বুঝলে তবেই কাব্যকে বোঝা সম্ভব। সুতরাং কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে -এক কথা রবীন্দ্রনাথ নিজ মুখে বললেও আমরা বলব কথাটা আংশিক সত্য-পুরোপুরি সত্য নয়। পুরোপুরি সত্য নয় এই কারণ যে কথাটা একতরফা। কবির যেমন বলার অধিকার আছে, কাব্যেরও তেমনি অধিকার আছে। কাব্যকে যদি জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কেমন করে জানব-কাব্য বলবে, কবিকে জানার চেষ্টা কর, তাঁকে বুঝলে আমাকেও বুঝতে পারবে। কবির জীবনই তাঁর কাব্যের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য টীকাগ্রন্থ। সেই জীবনকে যদি জীবনীর পাতায় জীবন্ত করে তোলা যায় তবে সেই জীবনীকারই হবেন কাব্যের প্রকৃষ্ট ভাষ্যকার। কবি নিজে যদি লেখেন তা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কাব্যের স্বরচিত ভূমিকা। পরবর্তীকালে সে কাহিনীরও আবার পরিশিষ্ট লিখেছেন-আত্মস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনীরও আবার পরিশিষ্ট লিখেছেন আত্মপরিচয় নামক গ্রন্থে। এ ছাড়াও বহু প্রবন্ধে, অগণিত চিঠিপত্রে তিনি নিরন্তর নিজের কথা বলেছেন। যে পরিবার পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন, যে শিক্ষা এবং শিল্পরুচি বালক বয়সে তিনি প্রতি মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, যে সব দৃষ্টান্ত চোখের সুম্মুখে দেখেছেন, যে সব অনুভূতিকে মুল্য দিতে শিখেছেন, যে আদর্শকে আপন মনে লালন করেছেন, যে ব্রত আজীবন পালন করেছেন সে সব কথা নানা সূত্রে নানা ভাবে কথায় এবং লেখায় প্রকাশ করেছেন। আপন কাব্যের সম্যক পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই আত্মপরিচয়ের এই প্রয়াস। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সম্পর্কে ঢ়ৎবষঁফব এর উল্লেখ আগেই করেছি। কীটস-কাব্যেরও প্রকৃত টীকাগ্রন্থ তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন।
কবির জীবনকাহিনীর ওপর এতখানি গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে কবির জীবনের মধ্যে যার প্রকাশ কাব্যেও তারই প্রকাশ। তাই যদি না হত তবে কাব্য শুধু মুখের বুলি হয়ে দাঁড়াত। প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনই কাব্য হয়ে ফুটে ওঠে। এখানে জীবন বলতে বুঝি কবির জীবনধর্ম, তাঁর স্বভাবধর্ম। বঙ্গবন্ধু যে অর্থে বলেছিলেন, my life is my message-আমার জীবনই আমার বাণী, ঠিক সেই অর্থেই কবিও বলতে পারেন, আমার জীবনই আমার কাব্য। এ কথা মানতেই হবে যে কবির আগে, কাব্য পরে। আগে কবিজীবন যাপন করতে হয়, কবিধর্ম পালন করতে হয়, তবেই কাব্য রচনা সম্ভব হয়। গোটা মানুষটার কতখানি অংশ কবি তাই দিয়ে কাব্যের মহিমা। ইংরেজ কবি স্ত্রী এবং পুরুষ প্রেমিকের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেচেন-Man’s love is of man’s life a thing apart, tis woman’s whole existenace। পৃথিবীর সুবৃহৎ কবি-সমাজেও কবিতে কবিতে পার্থক্যের অবকাশ আছে। সাধারণ অর্থে কবি নামে যাঁরা পরিচিত, বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে জীবনের খুব কম অংশেই এঁরা কবি। গোটা মানুষটার সামান্যতম অংশে কবিধর্মের ছাপ পড়েছে, কবিস্বভাবের পরিচয় আছে। অর্থাৎ কবিধর্ম এঁদের জীবনেa thing apart ফলে কালের বিচারে এঁরা শেষ পর্যন্ত মাইনর পোয়েট-এর পর্যায়ে পড়েন। আর পৃথিবীতে যাঁরা মহাকবির আখ্যা লাভ করেছেন তাঁদের বেলায় সেই কবিধর্ম-তাঁদের whole existence। এঁরা সর্বক্ষণ সর্বান্তঃকরণে কবি। সত্যিকারের যিনি কবি তাঁর কবিসত্তা এমন অবিসস্বাদিত রূপে ভাবে ভঙ্গিতে কথায় আচরণে সমস্ত দেহে মনে ফুটে উঠবে যে তাঁকে চিনতে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না। কবিপ্রকৃতি স্ব-প্রকাশ। নিজেকে কবি প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কবিতা আওড়াতে হয় না। কবিপ্রকৃতি স্ব-প্রকাশ। নিজেকে কবি প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কবিতা আওড়াতে হয় না। মানুষটা একেবারেই আর পাঁচ জনের মতো নয়। বাইরে থেকে দেখতে যতই সাধারণ মনে করে তাঁর সেই অনন্যতা কোনো ব্যক্তির চোখ এড়াতে হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে দেখে অশিক্ষিত সরাইঅলার মনে যে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তা এরই কোন কালে সে দেখেনিstandin by hisself and stopping agapin, with his jaws working the whoal time…. ye knit was poetry as did it. মানুষটা যে কবি ঐ অশিক্ষিত লোকটির দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছে। অপর দিকে গ্যেটেকে দেখে নেপোলিয়নের বিস্ময় অপর প্রান্তের আরেক দষ্টান্ত। দিগি¦জয়ী বীর-রাজা-উজির তো বটেই, জ্ঞানী-গুণিও অনেক দেখেছেন, কিন্তু গ্যেটেকে দেখে একেবারে যেন চমকে উঠলেন-যবৎব’ং ধ সধহ! এতদিনে দেখলেন মানুষের মতো মানুষ, পরিপূর্ণ মানব-অদ্বিতীয়, অনন্য। এ বিস্ময় কেন? গ্যেটের কবিপ্রতিভার দীপ্তি এবং কবিস্বভাবের লাবণ্য নিঃসন্দেহে মুখে চোখে জাজ্জ্বল্যমান ছিল,মুনের ঐশ্বর্য সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথকে দেখে চমকে ওঠেন নি এমন মানুষ কমই আছেন। সে যে কেবল তাঁর দেবদুর্লভ দেহকান্তির জন্য এমন নয়। এটি কবিমনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ইংরেজ সাহিত্যিক আর্নেষ্ট রীজ-এর উক্তি মনে পড়বে–For a moment I was abashed: it was as if the prophet Isaish had come to one’s door. . পরমুহূর্তেই বলেছেন -অথচ অত্যন্ত সরল সহজ মানুষটি, বসে বসে বড় বড় তত্ত্বকথা বলেন নি। খুব ঘরোয়া রকমের সাধারণ কথাই বললেন, চা খেলেন, বান পান খেলেন। অথচ গৃহে পদার্পণ মাত্র মনে হল যেন এক অভাবনীয় আবির্ভাব। মনে প্রাণে, সব অঙ্গে মনে কবি-সেই কারণেই মানুষকে এতখানি তিনি অভিভূত করতে পেরেছেন। কবিমনের ঐশ্বর্য মানুষকে অমোঘ শক্তিতে টানে।
সে ঐশ্বর্য সর্বব্যাপী, একমাত্র কাব্যরচনাতেই তার প্রকাশ-এমন নয়। কবিকে সব দেশেই বলা হয়েছে স্রষ্টা। স্রষ্টার মন অকৃপণ মন। সৃষ্টির প্রদান লক্ষণ তার অজস্রতা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে সৃষ্টিলীলা দেখছি তার অজস্রতা আমাদেরকে অভিভূত করে। চতুর্দিকে ঝরছে পড়ছে উড়ছে মরছে নষ্ট হচ্ছে অথচ কোথাও কিছুর কমতি নেই। এত অপব্যয়েও ভান্ডার সর্বদাই পূর্ণ। অপব্যয়ের ভয় নাহি তার পূর্ণের দান স্মরি। যাকে অপব্যয় মনে করি সে শুধু সৃষ্টির লীলা। এই যা কিছু মনে করছি নষ্ট হচ্ছে এ আর কিছু নয়-নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা উদ্বৃত্ত, যেটা না হলেও চলত সেই উদ্বৃত্তের মধ্যেই তার ঐশ্বর্যের প্রকাশ। সৃজনী মন অর্থাৎ কবির মনও এমনি ভরাট, কানায় কানায় পূর্ণ-খানিকটা সারাক্ষণই ছলাৎ করে উপচে পড়ছে। সেই উদ্বৃত্ত অংশ কাব্যে যতটুকু প্রকাশ পায় তার চাইতে বেশি পায় আলাপে ব্যবহারে, আচারে রুচিতে, চিন্তায় কর্মে। কারণ কাব্যের চাইতে জীবনের ব্যাপ্তি বৃহত্তর। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা এই উদ্বৃত্তের সাধনা।
মনের সম্পদ যে সব চাইতে বড় সম্পদ সে কথা বলাই বাহুল্য। কবিমনের স্পর্শমণিতে সমস্তই সোনা হয়ে ওঠে। সেটিই কবির আসল ঐশ্বর্য। অবশ্য এ কথা এমন সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে এর উল্লেখমাত্র নি®প্রয়োজন। কিন্তু যে কথাটার উল্লেখ প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সাংসারিক অর্থে আমরা যাকে ঐশ্বর্য বলি সে ঐশ্বর্যও রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। এখানে আবার সেই জীবনচরিতের প্রশ্নেই ফিরে আসতে হয়। ঐশ্বর্যবানের গৃহে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মোগল রাজত্বের অন্তিম পর্যায়ে-ব্রিটিশ আগমনের সুচনায় ঠাকুরবংশের অভ্যূত্থান। বাদশাহী আমলের হালচাল, জাঁকজমক এ পরিবারে প্রবেশ করেছিল। দ্বারকানাথের বিরাট ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথ দেখেননি কিন্তু তার যে ভগ্নাবশেষ তিনি দেখেছেন তারও তুলনা নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথের জীবনে যে রাজসমারোহ রবীন্দ্রকাব্যে সেই সমারোহের সুস্পষ্ট আভাস। পিতা দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি আখ্যা লাভ করেছিলেন, কিন্তু রাজর্ষি আখ্যা বোধকরি তাঁকে আরো বেশি মানাত। তিনি যথার্থই রাজপুত্র। যৌবরাজ্যে অভিষেক। মুহূর্তে তাঁর বনবাস-পিতার ঐশ্বর্য দেনার দায়ে নিঃশেষিত। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য অর্থাৎ পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথের দারিদ্র বরণ এবং আপন পৌরুষ বলে হৃত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধার জন্য দেবেন্দ্রনাথের দারিদ্র বরণ এবং আপন পৌরুষ বলে হৃত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধার-এ সবের মধ্যে আমাদের প্রচলিত রূপকথার আমেজ আছে। রাজর্ষি আখ্যা এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য যে রাজ-ঐশ্বর্য লাভ করেও নিরাসক্ত তাঁর মন। ত্যাগের মধ্যেই ভোগের আনন্দ লাভ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রগাঢ়তম প্রভাব। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যে রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছেন, ভিক্ষুবেশী রাজা অশোককে যে তিনি পুরুষোত্তমের আসন দিয়েছেন তার মূলে (রাজর্ষি) দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত। শিবাজীর প্রতি গুরু রামদাসের আজ্ঞা-রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন-মহর্ষির জীবনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর পক্ষে সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যে থেকেও-লভিব মুক্তির স্বাদ-এ সমস্তই মহর্ষিজীবনের প্রতিধ্বনি। জীবনের উপরিস্তরে রাজসমারোহ, অন্তস্তলে নিরাসক্তি-এ দুই জিনিসই রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক আবহাওয়া থেকে পেয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু ঐশ্বর্যের রূপ তাঁর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে (কবি মাত্রেরই মন ঐশ্বর্যবিলাসী)। এই কারণে জীবনে যা কিছু বৃহৎ মহৎ কামিনীয় এবং বরণীয় মনে হয়েছে তাকেই তিনি ঐশ্বর্যমন্ডিত রূপে দেখেছেন। দেবতাকে যখন আবাহন করেছেন, অন্তরতমকে চেয়েছেন তখন তাঁকেও দেখেছেন রাজা বেশে। বলেছেন-রাজাসমারোহে এস। তাঁর দেবতার আগমন স্বর্ণরথে-তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে / আমি মনে ভাবতেছিলাম এ কোন্ মহারাজ। / ‘মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে / গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা / হে রাজেন্দ্র, তব হাতেকাল অন্তহীন।
এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেয়া যায়। বরণীয় তা তো বটেই, যা কামনীয় তাকেও রাজা হিসেবেই দেখেছেন এবং রাজসমারোহ তাতে আরোপ করেছেন- রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে / প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
দেবতার বেলায় যেমন মানুষের বেলায়ও যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ দেখেছেন সে মানুষকেও তিনি রাজা হিসেবেই দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু কেবল মাত্র বাংলাদেশের স্থপতি নন, তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা। অগণিত মানুষের ওপর যাঁর বিপুল প্রভাব তিনিই যথার্থ রাজা। তাঁর গল্পে যে মানুষ প্রকৃত প্রেমিক, যে নারীর মনোহরণ করেছে সেও রাজা-অন্তর, অন্তর আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা। প্রেমের অভিষেক কবিতায় প্রথমেই বলে নিয়েছেন, তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।